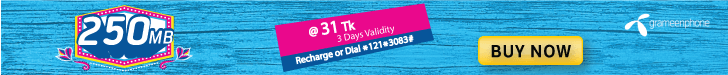আজ সোমবার দুপুর ১২:৩৯, ২রা ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
ক্ষমতায় থেকেও পদত্যাগ করতে বাংলাদেশে এর আগে কাউকে দেখা যায়নি

ক্ষমতায় থেকেও পদত্যাগ করতে বাংলাদেশে এর আগে কাউকে দেখা যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস। সম্প্রতি জিটিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন তিনি।
অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস বলেছেন, তরুণদের উদ্যোগেই বাংলাদেশে একটা রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ হলো এবং আত্মপ্রকাশের আগে যিনি আহবায়ক হয়েছেন নাহিদ ইসলাম, একটা বিরল ঘটনা তিনি ঘটিয়েছেন। এটা বিস্ময়কর আমার কাছে, এটা হচ্ছে যে, সে তার উপদেষ্টার পথ থেকে পদত্যাগ করেছেন। আমি কিন্তু বাঙালি মুসলমানদেরকে পদত্যাগ করতে দেখি না আসলে। কখনো মন্ত্রী হলে, উপদেষ্টা হলে, ডিজি হলে, কোন বড় পদে থাকলে সাধারণত তারা পদ থেকে ছাড়েন না। এই যে পদ ত্যাগ করা যা,য় না করা যায়, এইটা দেখেই নাহিদের প্রতি আমার আসলে সম্মান বেড়ে গেছে।
যে কোন একটা ভালো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, সে তার পদটাকে না করতে পেরেছে। এই যে না করতে পারা, এই যে ত্যাগ স্বীকার করতে পারা, এটাই কিন্তু এই নতুন দলের আত্মপ্রকাশের একটা নতুন তাৎপর্য হিসেবে আমি কিন্তু দেখছি আসলে।
তিনি বলেন, প্রথমে আমি এটা এপ্রিশিয়েট করছি। আর এই তরুণদের প্রতি আমার সবসময় আস্থা। তারা যখন উপদেষ্টা হয়েছিল, আমি কিন্তু বলেছিলাম, ইন্দোনেশিয়াতে এরকম সুকর্ণ নামে একজন খুবই কুখ্যাত স্বৈরাচারী ছিল। তার যখন পতন ঘটে এবং স্টুডেন্ট আন্দোলনের ফলে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টের মূল আন্দোলন করেছিল। এবং সেই ক্যাবিনেটে কিন্তু ছাত্রদের অংশীদারিত্ব ছিল। বাংলাদেশের ইতিহাসে কিন্তু প্রথমবারের মতো এরকম ছাত্রদের অংশীদারিত্ব নিয়ে কিন্তু একটা উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছিল। সেটাও আমি এপ্রিশিয়েট করেছি। এবং ও যে ওখান থেকে বাদ দিয়ে এসে এবং বাইরে যারা ছিল, সবাইকে নিয়ে যারা জুলাই গণঅভ্যুত্থানে দারুণভাবে অ্যাক্টিভ ছিল, কাজ করেছে এবং একটা স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে, তারা মিলে যে দলটা করেছে, আমার মনে হয় যে, ওরা কেবল এক সরকার থেকে আরেক সরকারের বদল দেখতে চায় না।
যেটা মানুষের আকাঙ্ক্ষা, আমাদের নিজেদেরও আকাঙ্ক্ষা, একটা বড় রাজনৈতিকের পরিবর্তন আমরা দেখতে চাই। একটা গুণগত পরিবর্তন দেখতে চাই। আমাদের পলিটিক্যাল কালচার কিংবা রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে নিম্নমান, এইটাকে একটু তুলে আনা যায় কিনা, সেই উদ্যোগ নিয়েই তারা দলটা করেছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এই অধ্যাপক বলেন, একটা কথা প্রায়ই আপনারা শুনবেন, আমরা সবাইকে বলতে শুনি যে, তরুণরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তা আমি এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি। এই ভবিষ্যৎ মানে হচ্ছে একটা মূল ঝুলিয়ে রাখে। তরুণদেরকে বলে যে এখন না, ভবিষ্যতে তোমরা হচ্ছে আসবে। আমি বলি না, তরুণরাই জাতির বর্তমান। এই তরুণরাই বর্তমান, এরাই স্বৈরাচারী হাসিনা এখান থেকে সরাতে বাধ্য করেছে এবং এই তরুণরাই কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক দলটা করেছে।
কাজেই প্রবাদটাকে পরিবর্তন করে আমাদের বলতে হবে, তরুণরাই জাতির বর্তমান। তারা হাত দিয়েছে এইটা। আমার তাদের প্রতি শুভকামনা রইল এবং এরা হচ্ছে অন্য পলিটিক্যাল পার্টি যারা আছে, যারা মাঠে বিরাজমান, তাদের প্রতি কিন্তু একটা চাপ থাকবে যে, এই ছাত্ররা কিন্তু মাঠে আছে। যারা একটা সফল আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং সফলতা পেয়েছে। এবং তারা যেভাবে শুরু করেছে, সেটা আমার ভালো লেগেছে। অনেকে ভয়ে ছিলেন যে, এরা কি আসলে একটা ধর্মীয়, একটা মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলে পরিণত হয় কিনা!
তিনি বলেন, এই আশঙ্কা অনেকের মধ্যে আছে। আমি দেখেছি কিন্তু, আমি দেখলাম যে না, অনুষ্ঠানের শুরু করলো কিন্তু চারটা প্রধান ধর্মের ধর্মগ্রন্থ থেকে কিন্তু তারা পাঠ করেছে। কাউকে বাদ দেয় নাই। কাজেই যে বহুত্ববাদী সমাজের কথা যে আমরা বলি, যে বাংলাদেশ কেবল বাঙালির না, বাংলাদেশ কেবল মুসলমানের না, বাংলাদেশের বাঙালি ছাড়াও আরো ৫০ টিরও বেশি জাতির মানুষ বাস করে। চাকমা, মারমা, পাঙ্খ, আলুসাই তাদেরও বাংলাদেশ। এখানে মুসলমান ছাড়াও হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, নানান বিশ্বাসের মানুষ আছে, তাদেরও বাংলাদেশ।
সেই আওয়াজটাও কিন্তু তারা শুরুতেই কিন্তু দিয়ে দিয়েছে তাদের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। এবং তাদের ঘোষণাপত্রের মধ্যে যতটুকু আমি বক্তব্য পেয়েছি, তারা একটা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ চায়। তারা একটা বহুত্ববাদী বাংলাদেশ চায় এবং একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ চায়। যেখানে সমস্ত ধরনের ধর্ম, রাজনীতি, বিশ্বাস, তারপরে হচ্ছে নারী প্রশ্ন, পুরুষের প্রশ্ন, আমাদের জাতি প্রশ্ন, ভাষা প্রশ্ন, এরকম একটা সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের স্বপ্ন তারা কিন্তু দেখছে।
রোবায়েত ফেরদৌস বলেন, বাংলাদেশ এটা বহু জাতির, বহু ধর্মের, বহু ভাষার, বহু সংস্কৃতির, একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ রাষ্ট্র হবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার এই যে বহুত্ববাদী নীতি, আমি মনে করি, দ্যাট ইজ দা বিউটি অফ ডেমোক্রেসি। সেই একটা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কিন্তু তাদের মধ্যে আমি দেখেছি। এবং আমরা বলি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ হচ্ছে টলারেন্স। সহনশীলতা, সবাই আমার মত হবে না, সবাই আমার মত চিন্তা করবে না, সবাই আমার ধর্ম বিশ্বাস করবে না।
অন্যরা যারা আছে, অন্য ধর্ম, অন্য চিন্তা, অন্য মতবাদের মানুষ যারা আছে, অন্য রাজনৈতিক কনভিকশনের লোকরা যারা আছে, তাদেরকে সহ্য করা, তাদেরকে রেস্পেক্ট করা। সবচেয়ে ভালো রাষ্ট্র হচ্ছে সেইটা, যেখানে ভিন্ন মতকে, ভিন্ন চিন্তাকে স্বীকৃতি দেয়, রেকগনিশন দেয়। তাও না পারা গেলে, অন্তত ভিন্ন মত, ভিন্ন চিন্তাকে যেন রেস্পেক্ট করে। সেটাও যদি না পারা যায়, অন্তত যেন টলারেট করে, টলারেন্স, এই সহনশীলতা।
এই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আরেকটা বড় উপাদান হচ্ছে পরমত সহিষ্ণুতা। যে আমি তোমার সঙ্গে দ্বিমত করতে পারি, কিন্তু তোমার কথা বলতে দেওয়ার জন্য আমি আমার জীবন দিতে পারি। এই পরমত সহিষ্ণুতা, পরধর্ম সহিষ্ণুতা, এটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রধান জায়গা।
সাংবাদিকতা বিভাগের এই অধ্যাপক বলেন, নির্বাচন তো একটা জায়গা, আমরা সারাক্ষণ বলি, তো নির্বাচনই মেইন কথা না। নির্বাচনের পরে যে সরকার আসবে, তারা কতটা সহনশীল। তারা কতটা সার্ভিস ডেলিভারি দিতে পারে, গুড গভর্নেন্স দিতে পারে কিনা। বাংলাদেশে কিন্তু ১৬ বছরে সীমাহীন দুর্নীতি হয়েছে, সীমাহীন লুটপাট হয়েছে, ২৮ লক্ষ কোটি টাকা পাচার হয়ে গেছে, ব্যাংকিং সেক্টরে সীমাহীন বিশৃঙ্খলা।
এই ভূমি অফিস যান, শিক্ষা অফিস যান, সচিবালয়ে যান, সাবরেজিস্ট্রার অফিসে যান, সর্বোচ্চ কিন্তু সীমাহীন দুর্নীতি। ওরা যেটা বলেছে, ওরা একটা দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ করতে চায়। এইটা হচ্ছে সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ, আদৌ তারা আসলে পারবে কিনা! তো এখনো কিন্তু আমরা দেখেছি, শেখ হাসিনা চলে যাওয়ার পরে, এই সরকারের অনেক মাস পার হয়ে গেছে।
তাও সাত-আট মাস তো হয়ে গেছে প্রায়, দুর্নীতি কিন্তু একটুও কমে নাই। করাপশনটা কিন্তু কমে নাই। সরকারি অফিসগুলোতে গভর্নেন্সের জায়গা, গভর্নেন্স, গুড গভর্নেন্সের মানে হচ্ছে যে, দক্ষ, যোগ্য, জনগণের অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া। এমন কোন দুর্নীতি এখানে থাকবে না, সেই ট্রান্সপারেন্সি, সেই একাউন্টেবিলিটি, সেটা কিন্তু এখনো আমরা দেখতে পাচ্ছি না।
তিনি আরো বলেন, কাজেই এই নতুন দল যারা আত্মপ্রকাশ করছে, তাদের মূল চ্যালেঞ্জের জায়গা হচ্ছে, কিভাবে দুর্নীতির মূল উৎপাটন করতে পারে। এবং যারা শাসক হবে, তাদেরকে চোখে চোখে রাখতে হবে। পুরা ওয়েস্টার্ন ডেমোক্রেসি টিকে আছে এক ধরনের জবাবদিহিতার কাঠামোর মধ্য দিয়ে। প্রত্যেকে প্রত্যেকে চোখে চোখে রাখে, পার্লামেন্ট বিচার বিভাগে, বিচার বিভাগ পার্লামেন্টকে, পার্লামেন্টকে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে ইউনিভার্সিটি, প্রত্যেককে প্রত্যেককে চোখে চোখে রাখে। এই চোখে চোখে রাখার মধ্য দিয়ে একটা একাউন্টেবিলিটি কিংবা একটা জবাবদিহিতা তৈরি হয়।
কাজেই একটা জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র কিন্তু আমাদের নির্মাণ করতে হবে। না হলে এই সংবিধান দিয়ে, এই রাজনৈতিক সংস্কার দিয়ে, আপনি যাদেরকেই সুষ্ঠ নির্বাচন হোক, অবাধ হোক, যে যারা আসবে, তারা স্বৈরাচার হতে বাধ্য। যে কারণে পলিটিক্যাল ফিলোসফারদের একটা মূল চিন্তাই ছিল যে, ক্ষমতাকে পাহারা দিয়ে রাখতে হবে। যেকোনো ক্ষমতার ঝুঁকি হচ্ছে স্বৈরাচারী হয়ে যাওয়া।
বাসায় কাজের তিনজন ছেলেকে রাখলে, প্রধান কাজের ছেলে বাকি দুজনের উপর খবরদারী করবে। কাজেই এমন একটা ব্যবস্থা সংবিধানের মধ্যে থাকতে হবে, আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে থাকতে হবে, যেন জবাবদিহিতা থাকে। কারো সীমাহীন ক্ষমতা থাকবে না, কারো অ্যাবসলিউট পাওয়ার থাকবে না, সারাক্ষণ তাকে একটা চেক এবং ব্যালেন্সের মধ্যে তাকে আনতে হবে।